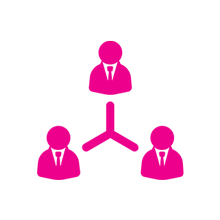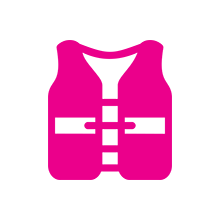২৩শে জুন থেকে ২৫শে জুন ১৯৮৯ ঢাকায় হোটেল সোনারগাঁওয়ে কমিশন অন হেলথ রিসার্চ ফর ডেভেলপমেন্ট এবং ব্র্যাকের উদ্যোগে এসেনশিয়াল ন্যাশনাল হেলথ ইনফরমেশন এ রিসার্চ বাংলাদেশ'-শীর্ষক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালার উদ্বোধনী অধিবেশনের সভাপতি তৎকালীন ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক স্যার ফজলে হাসান আবেদ যে ভাষণ প্রদান করেন তার অনুবাদ প্রকাশ করা হলো।
স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় উপ-প্রধানমন্ত্রী অধ্যাপক এম এ মতিন, অধ্যাপক ডেভিড বেল, অধ্যাপক লিঙ্কন চেন, উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ। বর্তমান শতাব্দী স্বাস্থ্যক্ষেত্রে নজিরবিহীন অগ্রগতি অবলোকন করছে। উন্নত বিশ্বে সংঘটিত এই অতি চমকপ্রদ অগ্রগতিকে দুটি অংশে ভাগ করা যায়। প্রথমত যা শতাব্দীর প্রথমার্ধে অর্জিত হয়েছে এবং দ্বিতীয়ত যা পঞ্চাশের দশক থেকে সূচিত হয়েছে ।
বর্তমান শতাব্দী স্বাস্থ্যক্ষেত্রে নজিরবিহীন অগ্রগতি অবলোকন করছে। উন্নত বিশ্বে সংঘটিত এই অতি চমকপ্রদ অগ্রগতিকে দুটি অংশে ভাগ করা যায়। প্রথমত যা শতাব্দীর প্রথমার্ধে অর্জিত হয়েছে এবং দ্বিতীয়ত যা পঞ্চাশের দশক থেকে সূচিত হয়েছে ।
প্রথমার্ধে যে অগ্রগতি হয়েছে তার পেছনে উন্নত জীবনযাপনের জন্য সামাজিক উদ্যোগের অবদান রয়েছে। এ সাফল্যে অর্থনৈতিক উন্নতি ও শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তবে দুধ পাস্তুরিতকরণ, ক্লোরিন ট্যাবলেট দিয়ে পানি শোধন, দাঁতের স্বাস্থ্যের জন্য ফ্লোরাইড ব্যবহার, উন্নত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, সুষম খাদ্যগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি, টিকাগ্রহণ, বিলম্বে গর্ভধারণ, খাদ্যে ভিটামিন ও আয়োডিন সংযুক্তি, প্রসবপূর্ব যত্ন, খাদ্য সংরক্ষণ শিক্ষা— এই সকল ব্যবস্থার অবদান তার চেয়ে কম নয়। ওপরে উল্লিখিত প্রতিটি ব্যবস্থা প্রয়োগের পর তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। প্রয়োগকৌশল পরিবর্তন করা হয়েছে এবং বিতর্কও উঠেছে। কিন্তু শতাব্দীর মাঝামাঝিতে ওপরে উল্লিখিত অধিকাংশ বিধিই শিল্পোন্নত দেশে নিয়মিত অনুশীলন করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অভিজ্ঞ ও মৌলিক বিজ্ঞানের জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ, কমিউনিটিতে কর্মরত প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রোগতত্ত্ববিদ, হাসপাতালের চিকিৎসক এবং অন্যরা এই উভয় গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন ও একযোগে কাজ করার ফলেই এই অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরপরই মনোযোগ অন্যদিকে ধাবিত হয়। ভেষজ বিজ্ঞান ও শল্য চিকিৎসায় নতুন অগ্রগতি এবং এন্টিবায়োটিকের মতো আশ্চর্য ওষুধ আবিষ্কারের ফলে এই মনোযোগ জনস্বাস্থ্যে দিক থেকে রোগ উপশম কার্যে (curative service ) চলে যায়। নতুন নতুন হাসপাতাল ও মেডিকেল স্কুল খোলা হয় এবং বড় বড় ওষুধ কারখানা গজিয়ে ওঠে। কার্যত মেডিকেল শিক্ষা পাঠ্যক্রম থেকে রোগ প্রতিরোধক বিষয় বাদ দেওয়া হয় এবং সরকারি স্বাস্থ্যনীতিতে জনস্বাস্থ্যের বিষয়টি কম গুরুত্ব পেতে থাকে।
কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরপরই মনোযোগ অন্যদিকে ধাবিত হয়। ভেষজ বিজ্ঞান ও শল্য চিকিৎসায় নতুন অগ্রগতি এবং এন্টিবায়োটিকের মতো আশ্চর্য ওষুধ আবিষ্কারের ফলে এই মনোযোগ জনস্বাস্থ্যে দিক থেকে রোগ উপশম কার্যে (curative service ) চলে যায়। নতুন নতুন হাসপাতাল ও মেডিকেল স্কুল খোলা হয় এবং বড় বড় ওষুধ কারখানা গজিয়ে ওঠে। কার্যত মেডিকেল শিক্ষা পাঠ্যক্রম থেকে রোগ প্রতিরোধক বিষয় বাদ দেওয়া হয় এবং সরকারি স্বাস্থ্যনীতিতে জনস্বাস্থ্যের বিষয়টি কম গুরুত্ব পেতে থাকে।
এ সবই ঘটেছে শিল্পোন্নত দেশগুলোতে। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কি ঘটেছে ? চল্লিশের দশকের শেষভাগে বা পঞ্চাশের দশকে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত এই দেশগুলোর একমাত্র কাজ ছিল শিল্পোন্নত দেশে প্রচলিত রোগ নিরাময় মডেল অনুসরণ করা। আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই যে ওই রোগনিরাময় মডেল উন্নয়নশীল দেশগুলোতে চালু করা হয়েছিল। সারকথা হলো গ্রামভিত্তিক জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের পর্যায়টি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। হাসপাতাল নির্মাণ, রোগনিরাময় বিষয়ে ডাক্তারদের ট্রেনিং দেওয়া— যা নিরাময়ভিত্তিক (curative) ব্যবস্থাকে সমর্থন জোগায় তা অগ্রাধিকার পেতে থাকে। রোগ প্রতিরোধক ওষুধ এবং রোগতত্ত্ব ভালোভাবে পড়ানো হয় না। যাও পড়ানো হয় তা মেডিকেল কলেজগুলোতেই পড়ানো হয়।
উদাহরণ সহকারে এই নীতির অশুভ ফলাফল দেখানো যায়। একটি উদাহরণ দিই। টিকা প্রদান অত্যন্ত স্বল্পব্যয়ের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা, যদিও ১৯৭৯ সালে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। তথাপি ১৯৮৪ সালে ২ শতাংশের কম শিশু স্বল্পব্যয়ের ও পরীক্ষিত ডিপথেরিয়া, লতাকাশ, ধনুষ্টংকার, হাম ও পোলিও রোগের টিকা নিয়েছে। অথচ এই রোগগুলো শিশুমৃত্যুর প্রধান কারণ। রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থার বর্তমান অবকাঠামো খুবই নড়বড়ে। গ্রামভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে জানাশোনাও কম। রোগের প্রাদুর্ভাব লিপিবদ্ধ করা এবং জন্ম-মৃত্যুর রেজিস্ট্রি করার কথা আছে কিন্তু সে তথ্য জানা যায় না। গ্রামভিত্তিক রোগের প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় না।
এটি পরিষ্কার যে আমাদের স্বাস্থ্যব্যবস্থা নির্মাণে আমরা শিল্পোন্নত দেশগুলোকে অনুসরণ করার চেষ্টা করছি। কিন্তু ওই দেশগুলো শতাব্দির প্রথমার্ধে যে কাজটুকু করেছিল, আমরা তা পাশ কাটিয়ে এসেছি। টেকসই উন্নয়নের জন্য আমাদের সেই প্রাথমিক কাজটুকু করতে হবে।  গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ কেন?
গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ কেন?
গবেষণাকে মনে করা হয় সমস্যা সমাধানের পদ্ধতিগত চেষ্টা। এটি ৪টি মৌলিক উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে। যথা—
ক) সমস্যা চিহ্নিতকরণ, যাচাইকরণ ও অগ্রাধিকার নির্বাচন।
খ) স্বাস্থ্যবিষয়ক নীতি, কর্মসূচি এবং প্রযুক্তি গ্রহণ ও প্রয়োগের অগ্রগতি।
গ) নতুন কৌশল ও উপায় উদ্ভাবন এবং জানার পরিধিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।
ঘ) বাস্তব সমস্যা সমাধানে গবেষণা সহায়তা করতে পারে নতুন উপায় (tool) উদ্ভাবনে এটা অত্যাবশ্যক এবং আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষমতা ও প্রতিশ্রুতি কাজে লাগাতে এটি সহায়ক। খাওয়ার স্যালাইন ডায়রিয়া চিকিৎসায় কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়েছে। ডায়রিয়ায় বাংলাদেশে প্রতিবছর হাজার হাজার শিশু মারা যায়।
গবেষণা এবং মাঠপর্যায়ে পরখ করার মাধ্যমে আমরা বাড়িতে বসে বাড়িতে প্রাপ্ত উপাদান দিয়ে সহজ উপায়ে সস্তা খাওয়ার স্যালাইন তৈরির পদ্ধতি পেয়েছি। তারপর এই পদ্ধতি বাংলাদেশের পল্লীর মায়েদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। ১৯৮০ সালে কর্মসূচির প্রথম পর্বের মূল্যায়ন করে একটি গুরুতর সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে। সমস্যাটি হলো ডায়রিয়ায় আক্রান্ত ১০ শতাংশেরও কম রোগীকে খাবার স্যালাইন দিয়ে চিকিৎসা করা হয়েছে যদিও মায়েরা সঠিকভাবে স্যালাইন তৈরি জানত। পরবর্তী গবেষণায় মায়েদের এরূপ আচরণের কারণ জানা গেছে। একটি কারণ হলো স্যালাইন তৈরির একটি উপাদান গুড় সব সময় পাওয়া যায় না। তারপর চিনি ও চালের গুঁড়ো দিয়ে স্যালাইন তৈরির আরেকটি গবেষণা চালানো হলো। স্যালাইনের গ্রহণযোগ্যতা পরীক্ষার জন্যই আমরা এ গবেষণা চালাই।
১৯৮০ সালে কর্মসূচির প্রথম পর্বের মূল্যায়ন করে একটি গুরুতর সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে। সমস্যাটি হলো ডায়রিয়ায় আক্রান্ত ১০ শতাংশেরও কম রোগীকে খাবার স্যালাইন দিয়ে চিকিৎসা করা হয়েছে যদিও মায়েরা সঠিকভাবে স্যালাইন তৈরি জানত। পরবর্তী গবেষণায় মায়েদের এরূপ আচরণের কারণ জানা গেছে। একটি কারণ হলো স্যালাইন তৈরির একটি উপাদান গুড় সব সময় পাওয়া যায় না। তারপর চিনি ও চালের গুঁড়ো দিয়ে স্যালাইন তৈরির আরেকটি গবেষণা চালানো হলো। স্যালাইনের গ্রহণযোগ্যতা পরীক্ষার জন্যই আমরা এ গবেষণা চালাই।
গবেষণা ও কর্ম পরিপূরক। যেখানে কর্মসূচি আজ নির্দিষ্ট কিছু লোকের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য মনোনিবেশ করে সেক্ষেত্রে গবেষণা ভবিষ্যতের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর বহুমুখী উন্নতির জন্য একটি বিনিয়োগ ।
গবেষণা অর্থ বাঁচাতে সহায়তা করতে পারে। সমস্যার অগ্রাধিকার নির্ণয়ে এবং স্বাস্থ্যনীতি ও কর্মসূচির দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে গবেষণা সহায়তা করে।
প্রায়ই মনে করা হয় যে, গবেষণা হলো একটি কেতাবি ব্যাপার এবং জরুরি স্বাস্থ্যচাহিদা পূরণের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। কেউ কেউ মনে করেন গবেষণা একটি বিলাসিতা যা উদ্বৃত্ত সম্পদের অধিকারীরাই শুধু করতে পারেন। অন্যরা মনে করেন গবেষণার ফলাফল খুব কমই কাজে লাগে এবং কখনও সময়মতো কোনো এনজিও বা মন্ত্রণালয়ের কাজে তা লাগানো যায় না।
অনেক দাতা সংস্থা কোনো কর্মসূচিতে অর্থ জোগান দেবার সময় গবেষণা খরচ বাদ দিয়ে দেন। এসবই গবেষণা সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা। এভাবে গবেষণার অবদানকে দারুণভাবে অবমূল্যায়ন করা হয়েছে, যার প্রেক্ষিতে ‘উন্নয়নের জন্য স্বাস্থ্যগবেষণা কমিশন’ গঠন করা হয়েছে।
এটি একটি স্বাধীন আন্তর্জাতিক প্রয়াস এবং এতে স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন বিষয়ে অনেক দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব রয়েছেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এই কমিশনের একটি ক্ষুদ্র কিন্তু দক্ষ সচিবালয় রয়েছে এবং কমিশনের প্রধান হচ্ছেন অধ্যাপক লিঙ্কন চেন। তিনি আজ আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন।
স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সহায়তার জন্য এই কমিশন দু'ধরনের গবেষণা চিহ্নিত করেছে–
ক) অতি প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যতথ্য ও গবেষণা এবং
খ) অগ্রাধিকার নির্ণয় করে আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যগবেষণা।
এই কর্মশালার উদ্দেশ্য হলো— এই অঞ্চলের উন্নয়নশীল দেশগুলোর জাতীয় অত্যাবশ্যক স্বাস্থ্যবিষয়ক তথ্য ও গবেষণার ব্যাপারে আলোচনা করা এবং আপনাদের বিশেষজ্ঞ মতামত চাওয়া।
বর্তমানে জ্ঞান ও প্রযুক্তির সৃষ্টিশীল প্রয়োগের মাধ্যমে অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশে অনেক কিছুই অর্জিত হতে পারে। বাংলাদেশসহ প্রতিটি দেশেরই প্রয়োজন হলো স্বাস্থ্যসমস্যা চিহ্নিতকরণ, সমাধানে অগ্রাধিকার নির্বাচন এবং নিজ পরিবেশের উপযোগী স্বাস্থ্যনীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন করা। দেশবাসীর স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধানে দেশের সম্পদ একত্র করতে হবে, বর্তমান স্বাস্থ্যবিষয়ক জ্ঞান ও প্রযুক্তির সর্বাধিক ব্যবহার করতে হবে অধিক ফললাভের জন্য। বুদ্ধিদীপ্ত ও পরীক্ষামূলক কাজ নিরলসভাবে চালিয়ে যেতে হবে।
দেশবাসীর স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধানে দেশের সম্পদ একত্র করতে হবে, বর্তমান স্বাস্থ্যবিষয়ক জ্ঞান ও প্রযুক্তির সর্বাধিক ব্যবহার করতে হবে অধিক ফললাভের জন্য। বুদ্ধিদীপ্ত ও পরীক্ষামূলক কাজ নিরলসভাবে চালিয়ে যেতে হবে।
এটি করতে হলে প্রতিটি দেশের নিজস্ব গবেষণা ক্ষমতা থাকতে হবে, নিজস্ব বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের উপযোগী স্বাস্থ্যনীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন, পরীক্ষা এবং মূল্যায়ন করতে হবে।
এই বিষয়গুলো আলোচনার জন্য গত জানুয়ারি মাসে ঢাকায় আমরা একটি করেছিলাম প্রাথমিক সভার আয়োজন করেছিলাম। ওই সভায় স্বাস্থ্যবিষয়ক বিশিষ্ট পেশাদার ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন এবং এই কর্মশালা তারই পরবর্তী পদক্ষেপ।
আগামী তিনদিন আমরা এই বিষয়ে আলোচনা চালাব। আশা করি, বাংলাদেশে স্বাস্থ্যগবেষণা চালাতে গ্রহণযোগ্য, আর্থিক ব্যয়ভার বহনে সক্ষম এবং সরবরাহের দিক থেকে উপযোগী ফলাফল পাব। যার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন।
ধন্যবাদ ।
Last modified on Monday, 26 April 2021 19:31
কমিশন অন হেলথ রিসার্চ ফর ডেভেলপমেন্ট এবং ব্র্যাকের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক স্বাস্থ্যগবেষণা কর্মশালায় স্যার ফজলে হাসান আবেদের ভাষণ
Published in
Speeches and Presentations
Latest from
- BRAC and USAID launch the Bangladesh America Maitree Project to enhance the capacity of local NGOs
- নবম ‘ব্র্যাক মাইগ্রেশন মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড’
- BRAC Academy launches in Bogura
- MoU signed for economic inclusion and social protection for the marginalised communities
- BRAC welcomes Divya Bajpai as Executive Director of BRAC in Europe
Join the world’s biggest family